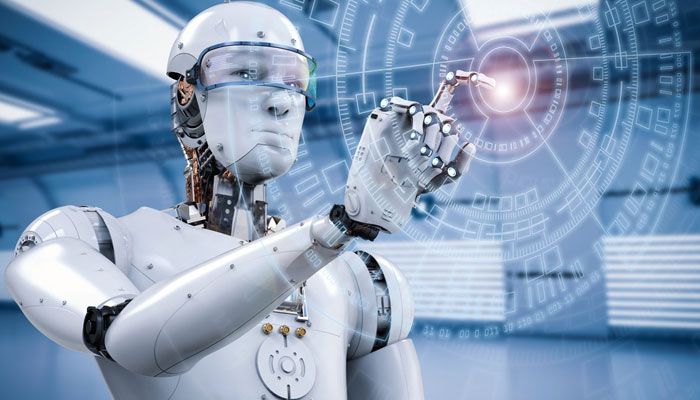তথ্যের এই যুগে অপতথ্য বা ভুল তথ্যই এখন সবচেয়ে বিপজ্জনক অস্ত্র। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অপতথ্য দিয়ে তৈরি করা ছবি ও ভিডিও বাংলাদেশে বড়ো ঝুঁকি তৈরি করেছে। এআই প্রযুক্তির ব্যবহার করে তৈরি করা অপতথ্য সংবলিত নানা ভিডিও এবং ছবি সমাজে নানা ধরনের বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। আমাদের দেশে ডিজিটাল লিটারেসি অনেক কম; তাই এআই সৃষ্ট কনটেন্টগুলো মানুষ সহজে বিশ্বাস করে। ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের প্রায় ৮০ শতাংশ পোস্টই এআই রিকমেন্ডশনে তৈরি। এ ছাড়া বিগত ৬ মাসে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অপতথ্য ছড়িয়েছে প্রায় দুই’শ গুণ। সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে, আর সত্যের জায়গা নিচ্ছে অসত্য তথ্যনির্ভর মিথ্যাচার।
গত ২ জুলাই এক সভায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস অপতথ্যের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, ‘ভুল বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথ্য শুধু জনমতকে বিভ্রান্ত করে না, বরং রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা ও সামাজিক শান্তিকেও বিঘ্নিত করে। অপতথ্য প্রতিরোধে কেবল রাষ্ট্র নয়, সাধারণ মানুষেরও সচেতন ভূমিকা থাকতে হবে। গণমাধ্যম, প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করেই একটি টেকসই ও নৈতিক তথ্যব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব উল্লেখ করে অপতথ্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান প্রধান উপদেষ্টা।
বাংলাদেশে প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) একদিকে যেমন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে, অন্যদিকে তা হয়ে উঠেছে অপপ্রচারের এক নতুন অস্ত্র। ভুল বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথ্য দিয়ে তৈরি করা কনটেন্ট শুধু জনমতকে বিভ্রান্ত করছে না,এর মাধ্যমে সমাজে বিভাজন তৈরি হচ্ছে এবং বিশৃঙ্খলা ও ক্ষতি ডেকে আনছে। অসৎ উদ্দেশ্যে সামাজিক অস্থিরতার সময়ে এআই সৃষ্ট ভুয়া ছবি, ভিডিও এবং মনগড়া বিশ্লেষণ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। সাইবার অ্যান্ড জেন্ডার-বেসড ভায়োলেন্স ইন বাংলাদেশ পর্যবেক্ষণে এ বছরের প্রথমার্ধে এআই-চালিত ডিজিটাল সহিংসতার শিকারদের মধ্যে ৭৬ শতাংশ নারী, যাদের অনেকেই রাজনীতিতে সক্রিয়। অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের জরিপে দেখা গেছে, ৬৪ শতাংশ নারী অনলাইনে এ প্রযুক্তির মাধ্যমে হয়রানির শিকার হয়েছেন, যার মধ্যে ৭০ শতাংশই হচ্ছে শ্লীলতাহানিমূলক কনটেন্ট। বর্তমানে এআই ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও সাইবার ব্ল্যাকমেইলের ক্ষেত্রেও ব্যবহার হচ্ছে, যা জনগণের নাগরিক মানবাধিকার ও সাংবিধানিক অধিকারকে হুমকির মুখে ফেলছে।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহার এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই)’র দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ দেশ ও সমাজ। নানা সমালোচনা থাকলেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে অগ্রাহ্য করার সুযোগ নেই। বর্তমানে ইউটিউব একদিকে যেমন জনপ্রিয় হয়েছে তেমনি আয়ের একটি প্ল্যাটফর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের লাখ লাখ মানুষ ইউটিউবে কনটেন্ট তৈরি করে মাসে হাজার হাজার ডলার আয় করছেন। ইউটিউবে এক হাজার ভিউ থেকে আয় হয় প্রায় ৫৫ টাকা থেকে ৫৫০ টাকার মতো। ভিডিওর থাম্বনেল যত আকর্ষণীয় হচ্ছে, মানুষের আগ্রহ এবং ভিউ তত বাড়ছে । ভিউ বাড়লে কনটেন্ট ক্রিয়েটরের আয়ও বাড়ে। এখানে নীতি-নৈতিকতা, সত্য-মিথ্যার তেমন বালাই নেই।
বাংলাদেশে সক্রিয় মোবাইল সংযোগ সংখ্যা কম-বেশি ১৮ কোটি ৫০ লাখ,যা দেশের মোট জনসংখ্যার ১০৬ শতাংশের মতো। দেশে অনেকেই একাধিক মোবাইল সিম ব্যবহার করছে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা কম-বেশি ৭কোটি ৭০ লাখ। দেশের মোট জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশেরও বেশি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করছে ৬ কোটিরও বেশি মানুষ। এ সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় নেগেটিভ কনটেন্ট বেশি অর্গানিক রিচ হয়। নেগেটিভ তথ্য যদি প্রকৃত সংবাদের তুলনায় বেশি রিচ হয় অর্থাৎ বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে তাহলে মানুষ সেটিকেই গ্রহণ করে। বাংলাদেশের মতো একটি দেশে কোটি কোটি ফেক কনটেন্ট তৈরি হয়েছে, যা আসলেই উদ্বেগের। ফ্যাক্ট চেকার সংস্থা ডিসমিসল্যাবের এক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এ বছরের জুন-জুলাইয়ে প্রায় ৭০টির বেশি এআই দিয়ে তৈরি রাজনৈতিক ভিডিও প্রকাশিত হয়েছে। যার মোট দর্শক ভিউ ২৩ মিলিয়নেরও বেশি। এসব ভিডিওতে নারী, রিকশাচালক, ফল বিক্রেতা সবাইকে কল্পিত চরিত্রে দেখিয়ে জামায়াত, বিএনপি বা আওয়ামী লীগের সমর্থক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এমনকি সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নিয়েও আজগুবি ভিডিও ছড়ানো হয়েছে।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তির দ্রুত প্রসার অনেক ক্ষেত্রেই জীবনকে সহজতর করলেও, বাংলাদেশে এর অপব্যবহার ব্যাপকভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এআই টুলস ব্যবহার করে ফটোশপ ও জেনারেটিভ ফিল দিয়ে স্ক্রিনশটের তারিখ পরিবর্তন করে সহজেই বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে । এ ছাড়া এআই দিয়ে পুরো ফেসবুক পোস্টেও ভুয়া ইন্টারফেস বানানো যায়। যার মাধ্যমে পোস্টটি যে কোনো দিনের বা তারিখের বানানো সম্ভব। এসব বিভ্রান্তিকর কনটেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহরিত এআই টুলগুলো হচ্ছে, ডিপফেইসল্যাব, সিনথেটিকসহ আরও কয়েকটি। এগুলো খুবই সহজলভ্য। যা মাত্র ২৪ ডলারে কিনতে পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষও এখন এসব টুল ব্যবহার করে বাস্তবের মতো মুখভঙ্গি, কণ্ঠস্বর ও আচরণ নকল করতে পারছে। ফলে বিশ্বাসযোগ্য করে অপতথ্য তৈরি এবং মার্কেটিং করা খুব সহজ হয়ে গেছে।
নির্বাচনি মৌসুম সবসময় গুজব ও প্রোপাকান্ডার জন্য উর্বর ভূমি। অতীতে প্রার্থীদের নিয়ে ভুয়া খবর বা মনগড়া কেলেঙ্কারি ছড়ানো হয়েছে। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও এধরনের অপতথ্য ছড়ানোর সম্ভবনা রয়েছে। এজন্য সংশ্লিস্ট সকলকে সচেতন থাকতে হবে এবং জনগণকে এ বিষয়ে সচেতন করতে হবে। বাংলাদেশে ইতোমধ্যেই অনলাইন গুজব সহিংসতায় রূপ নিয়েছে। আমাদের সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি হলো আস্থার অবক্ষয়। যখন নাগরিকরা সত্য মিথ্যা আলাদা করতে পারে না, তখন তারা সত্য বা বৈধ সংবাদকেও সন্দেহের চোখে দেখে। ফলে শুরু হয় বিভ্রান্তি। ঐ সব বিভ্রান্তি থেকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ,নাগরিক মানবাধিকার ও সাংবিধানিক অধিকারকে হুমকির মুখে ফেলে,যা কোনভাবেই কাম্য নয়।
এআই-এর ইতিবাচক দিক সবচেয়ে বেশি বলেই জনগণ এটিকে গ্রহণ করছে। এআই যেহেতু সবার জন্য; তাই এই টেকনোলজির গতি অনুযায়ী সবাইকে চলতে হবে। এআই-এর মতো প্রযুক্তি, যা হতে পারত তথ্য যাচাইয়ের সহায়ক, তা-ই এখন হয়ে উঠেছে বিভ্রান্তি তৈরির হাতিয়ার। দেশের নাগরিকদের প্রযুক্তিগত শিক্ষার হার কম-বেশি ১০ শতাংশ ,তাই অধিকাংশ মানুষ না বুঝেই এআই সৃষ্ট ভুয়া ভিডিও সহজেই বিশ্বাস করছে। যদিও এআই সোশ্যাল বট ব্যবহার করে যে কোনো ফেসবুক পেইজ কিংবা ওয়েবসাইটকে সাময়িক অথবা পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব। কিন্তু এটাতো স্থায়ী কোনো সমাধান না।
আইনগতভাবে এআই-চালিত ভুয়া কনটেন্টকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে হবে। দেশে এআই প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্টে নির্দেশনা দেওয়া আছে। যদিও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলো চাইলে এই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারে। তার পরও সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্টের আওতায় এআই প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো এবং বিচার প্রক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত দক্ষ জনবল ও প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল সাপোর্টের ঘাটতি রয়েছে। এছাড়াও ভিজিল্যান্স টিম এবং টেকনোলজি এক্সপার্টস প্রয়োজন। প্রযুক্তিগতভাবে ডিপফেক ভিডিও শনাক্ত করার জন্য উন্নত টুল চেইনভিত্তিক তথ্য যাচাই ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। প্লাটফর্মে ইঞ্জিন এআই তৈরি কনটেন্ট সহজেই ধরতে পারে। এআই মার্কিং কনটেন্টে পুশ অ্যালার্ট দিলে ভিডিওটি এআই দ্বারা তৈরি কি না, তা সহজেই শনাক্ত করা যায়। টেকনিক্যাল এ বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে এবং জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে কনটেন্ট তৈরি ও মার্কেটিং এর সাথে ব্যক্তিদের।অপতথ্য মোকাবেলায় নাগরিক সচেতনতার বিকল্প নেই। এ সমস্যার সমাধান ব্যক্তি, পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম এবং রাষ্ট্রসহ সব স্তরের সম্মিলিত উদ্যোগে নিতে হবে। সবাইকে সবার আগে তথ্য নয় সত্য যাচাই করতে হবে। বিশেষ করে ব্যবহারকারীদের তথ্য যাচাইয়ের অভ্যাস গড়তে হবে। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে সতর্কতা ও মিডিয়া লিটারেসি বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে সাইবার অপরাধ দমনে কঠোর আইন প্রয়োগ, অনলাইনে নজরদারি এবং কমিউনিটি পর্যায়ে রিপোর্টিং সিস্টেম চালু করতে হবে। সরকারি পর্যায়ে দ্রুত ফ্যাক্ট চেক ও জনসচেতনতামুলক প্রচার চালাতে হবে এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কোম্পানিগুলোকেও দায়বদ্ধতার মধ্যে আনতে হবে। হবে। ভুল তথ্য ছড়ালে শুধু অনলাইন নয়, বাস্তব জীবনেও তার পরিণতি ভয়ংকর হতে পারে এ বার্তাটি স্পষ্টভাবে সবার কাছে পৌঁছে দিতে হবে। অপতথ্য প্রচারকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিচারের মুখোমুখি করে শাস্তি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি সরকার, গণমাধ্যম ও প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্মগুলোকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। তবেই সুফল পাওয়া যাবে।
লেখক: ইমদাদ ইসলাম
জনসংযোগ কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়
পিআইডি ফিচার